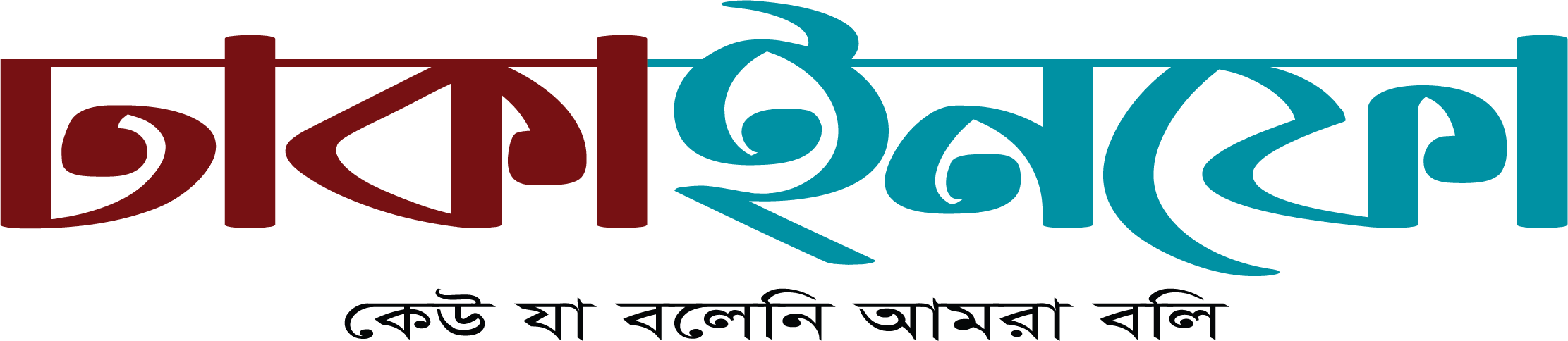বক্তা হিসেবে আমার কিছু উপদেশমূলক কথা বলা উচিত; কিন্তু উপদেশের চাইতে উদাহরণেই আমার বেশি বিশ্বাস। নীতিকথার পরিবর্তে মানুষের যাপিত জীবনে নীতির প্রতিফলনকে আমি বেশি গুরুত্ব দিই। আমি বরং শিক্ষা নিয়ে আমার কিছু ভাবনা, সমাজ নিয়ে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ এই বক্তৃতায় উপস্থাপন করব। আদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতারা শিক্ষার্থীদের ভেতর ঐক্য ও শৃঙ্খলা থাকার কথাটি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই ঐক্য ধর্ম, বর্ণ বা বিত্ত, শ্রেণিনির্বিশেষে সামাজিক হলেও এটি কখনো চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল না। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে পারে না; বরং চিন্তা যত বেশি বিবিধ ও বিচিত্র হয়, যত বহু পথে, বহু মতে পরিব্যাপ্ত হয়, তত এর শক্তি বাড়ে। কিন্তু আমাদের দেশের এবং সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কয়েকটি প্রকোষ্ঠে জ্ঞানকে বিষয় নির্দিষ্ট করে বিশেষজ্ঞ তৈরিতে মনোনিবেশ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরীক্ষা ও ছক বাঁধা গবেষণা কার্যক্রম, ঘণ্টা মেপে পাঠ সমাপনের আয়োজন।
ফলে একদিকে যেমন বিষয় অনুযায়ী চিন্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অর্থাৎ পাঠ্যবইকেন্দ্রিক তথ্য সবাই জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেন, তা দিয়েই চিন্তাকে সাজাচ্ছেন। অন্যদিকে পাঠ্য বিষয়ের বাইরে অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে না। কারণ, আমাদের প্রচলিত শিখন ও শিক্ষাপদ্ধতি তা হতে দেয় না। চিন্তার গভীরতা, বৈচিত্র্য, গতিশীলতা এবং দূরগামিতা না থাকলে নতুন জ্ঞান তৈরি হয় না।
আমরা ভালো মানের পরীক্ষার্থী তৈরিতে যতটা উদ্যোগী, শিক্ষার্থী তৈরিতে ততটাই অমনোযোগী। চিন্তার বিষয়টিকে আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক এবং এ ব্যাপারে আমি সহায়তা নেব যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রখ্যাত লেখক ও প্রকৃতিবিদ রালফ ওয়াল্ডো এমারসনের। এমারসনের মতে এক মানুষের ভেতরে আছে বহু মানুষ। এক মানুষ ধারণ করে বহু মানুষের চেতনা, সম্ভাবনা ও শক্তি। সমাজ অবশ্যই মানবিক সম্প্রসারণের পক্ষে থাকে না; বরং সংকোচনের পথে যায়। ফলে মানুষ তার সম্ভাবনা ও সক্ষমতাগুলো সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। একটি ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলতে দেখে।
পাহাড়ের মতো বাজার
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কি নতুন চিন্তা তৈরিতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করে? চিন্তার সঙ্গে চিন্তার সৃষ্টিশীল দ্বন্দ্ব এমনকি ঠোকাঠুকির পরিবেশ তৈরি করে? পাথরে পাথরে যে রকম ঠোকাঠুকিতে জ্বলে ওঠে আগুন, যাকে আমরা বলি জ্ঞান, যে জ্ঞান অন্ধকারে পথ দেখায়।
আমাদের উচ্চশিক্ষায় জ্ঞানভিত্তির সংকীর্ণ সংজ্ঞাটি—যাতে জীবনবাস্তবতা, ঐতিহ্য, লোকপ্রজ্ঞা অনুপস্থিত, তা আমাকে কষ্ট দেয়। একে তো জ্ঞানকে আমরা সনদের ওজনে মাপতে শুরু করেছি। তার ওপর গবেষণাকে পশ্চিম অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রকাশনা শব্দের অধীনে এনে দেশীয় জ্ঞানকে গৌণ অবস্থানে ঠেলে দিয়েছি। এখন বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সাধারণত চাকরিতে স্থায়ী হওয়া এবং পদোন্নতি পাওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত। এর একটি কারণ আমাদের উচ্চশিক্ষার সামনে–পেছনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বাজার। এই বাজারের ভেতর চাকরি আছে, চাকরির বাজার আছে; যার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত রূপটি সরকারি চাকরি। আরও আছে করপোরেট বাজার, মিডিয়া বাজার এবং নানা পরিষেবাসহ ছোট-বড় অনেক বাজার। পুঁজিশাসিত সমাজ মাত্রই নানাবিধ বাজার দ্বারা শাসিত হবে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে, প্রথমত খোলাবাজার অর্থনীতি এবং পুঁজির শাসনকে আমরা গ্রহণ করলেও এর বিপদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা আমাদের এখনো তৈরি হয়নি; এবং দ্বিতীয়ত বাজার বিষয়টা নিয়ে রয়েছে আমাদের ধারণাগত অস্পষ্টতা।
কোথায় ঘাটতি
আমাদের সমস্যা হচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায় থেকে আমরা মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী পরীক্ষার্থী তৈরি করছি। যে দুটি অঞ্চল থেকে নীতিনিষ্ঠতা ও মানবিকতার সূত্রগুলো তারা পাবে এবং সেগুলো জীবনে প্রয়োগ করবে, সে দুটি অঞ্চল আমরা ক্রমাগত তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। এর একটি হচ্ছে সংস্কৃতি, অন্যটি সমাজ। সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা হচ্ছে নিরন্তর পরিশুদ্ধতার চর্চা। যে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনো সাহিত্য পড়েনি, লোকসাহিত্য যার নাগালের বাইরে; যে সংগীত, চিত্রকলা, প্রকৃতিপাঠে কোনো দিন প্রবেশাধিকার পায়নি, তার অন্তর্গত সুচিন্তা ও ঔদার্যের সঙ্গে মিলিয়ে নীতিনিষ্ঠতা আর মানবিকতা বিকশিত হবে না; বরং ছক বাঁধা শিক্ষাক্রম তাকে সেসব ভুলিয়ে দেবে। তাকে বাজারের হিসাবে তার চিন্তাভাবনাকে মেলাতে উৎসাহিত করবে। একসময় সুচিন্তা ও ঔদার্যেও তার ঘাটতি পড়তে পারে।
আমাদের সমাজ থেকে সুনীতি যে চলে যাওয়ার পথে আছে, তার মূলে রয়েছে আমাদের শিক্ষার ন্যায়নিষ্ঠতার চ্যুতি। সমাজ—যার কাঠামোটি গড়ে দেয় পরিবার; একসময় নীতিনিষ্ঠতার চর্চাকে উৎসাহিত করত; কিন্তু সমাজ যত বস্তুগত উন্নতির দিকে গেল, অর্থাৎ বাজারের কবজায় চলে গেল, তত তার নীতিনিষ্ঠতায় ভাঙন ধরতে থাকল।
এখন অনেক পরিবারেও দুর্নীতি নিরুৎসাহিত হয় না। সেটি সম্ভব যদি হতো, সমাজটাকে আমরা অন্তত একটি ভরসার জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে পারতাম। যদি পরিবারগুলো সুনীতিকে একটি চর্চা হিসেবে টিকিয়ে রাখত, যদি ধর্মাচারের সঙ্গে ধর্মের নীতি ও সৌন্দর্যবোধকেও গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হতো, যদি সেবাধর্মিতা ও স্বেচ্ছাশ্রমকে উৎসাহিত করা হতো, যদি প্রকৃতিকে জীবনযাপনের সমান্তরাল করা যেত! একসময় সমাজ এ কাজগুলো করত। সে জন্য এর পরিচয়টা ছিল মানবিক। এই মানবিকতা একেবারে হারিয়ে যায়নি। এর পুনরুদ্ধার সম্ভব এবং সম্ভব শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে।
যদি পশ্চিমা জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের জ্ঞান যোগ করে শিক্ষাকে প্রকৃত বাঙালির করে তুলতে পারি, তাহলে এটিই হবে সত্যিকারভাবে সর্বজনীন, কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক এবং যুগোপযোগী। আমার বিশ্বাস, যেকোনো কর্মক্ষেত্রকেই আপনারা বেছে নিন না কেন, আপনাদের স্বকীয়তাকে এই লক্ষ্যে কিছুটা হলেও পরিচালনা করবেন।
আপনাদের চলার পথ বাধাহীন হোক, সবার জীবন আনন্দময় হোক—এই কামনা করি।